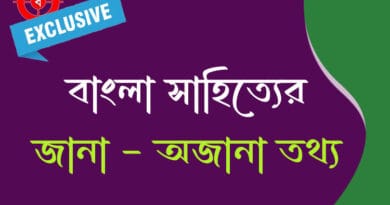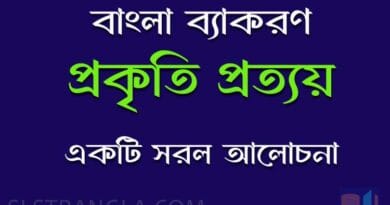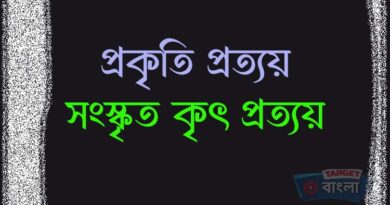উপসর্গ – সামগ্রিক আলোচনা
বাংলা ভাষার শব্দগঠনের দুটি প্রধান কৌশল হল প্রত্যয় যোগ ও উপসর্গযোগের মাধ্যমে নতুন শব্দ তৈরি। এছাড়া সন্ধি, সমাস, এককথায় প্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমেও নতুন শব্দগঠন করা যায়। আমাদের আজকের আলোচনা উপসর্গ। আজ এই আলোচনার প্রথম পর্ব। প্রথমে দেখে নেওয়া যাক উপসর্গের সংজ্ঞা ও কিছু তথ্য।
উপসর্গ কী ?
যেসব অব্যয় বা অব্যয়স্থানীয় ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ স্বাধীন পদ হিসাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু অন্য ধাতু বা শব্দমূল ও শব্দের পূর্বে বসে সেই ধাতু ও শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে তাকে উপসর্গ বলে। উপসর্গগুলি শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ তৈরি করে, অর্থের উৎকর্ষ দান করে, কখনও বা অর্থের সংকোচন ঘটায়। যেমন ‘বাঙালি’ এই বিশেষ্য পদটির পূর্বে ‘অ’ উপসর্গটি যুক্ত হয়ে ‘অবাঙালি’ শব্দটি তৈরি হয় যা মূল শব্দটির বিপরীতার্থক অর্থ প্রকাশ করে।
কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
➢ উপসর্গের অন্য নাম আদ্য প্রত্যয়।
➢ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর “ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ” গ্রন্থে উপসর্গকে ‘শব্দের আদিতে অবস্থিত তদ্ধিত প্রত্যয়’ বলেছেন।
➢ উপসর্গ শব্দটির ব্যুৎপত্তি – উপ + √ সৃজ্ + অ।
➢ ইংরাজি ভাষার Prefix এবং বাংলা ভাষার উপসর্গ একই রকম।
➢ ‘প্রতি’ ও ‘অতি’ উপসর্গ দুটির স্বাধীন প্রয়োগ দেখা যায়।
➢ ‘আম’ একটি বিদেশি উপসর্গ যার অর্থ সাধারণ। কিন্তু আম শব্দটি যখন ফলের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন সেটি একটি শব্দ।
➢ এটি ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব অংশের অন্তর্গত।
➢ সংস্কৃত উপসর্গগুলি সাধারণত ধাতুর পূর্বে বসে। অন্যদিকে বাংলা ও বিদেশিগুলি বিশেষ্য বা বিশেষণের পূর্বে বসে।
➢ ‘নি’ ও ‘আ’ উপসর্গ দুটি সংস্কৃত ও বাংলা উভয় তালিকাতেই আছে। এর কারণ তৎসম শব্দ তৈরির সময় সংস্কৃত ‘নি’ ও ‘আ’ উপসর্গ দুটি ব্যবহৃত হয়। আর বাংলা ‘নি’ ও ‘আ’ উপসর্গ দুটি তদ্ভব বা দেশজ শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
➢ বাংলা ভাষায় গৃহীত ২০টি সংস্কৃত উপসর্গের তালিকা – “প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অন্, নির্, (নিঃ) দুর্ (দুঃ), বি, অধি, সু, উদ্, পরি, প্রতি, উপ, আ, অপি, অভি, অতি।
একই শব্দের পূর্বে ব্যবহার
‘হার’ শব্দটির পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ বসিয়ে সৃষ্ট শব্দ। যেমন – আ + হার = আহার, বি + হার = বিহার, প্র + হার = প্রহার, সম্ + হার = সংহার, উপ + হার = উপহার, পরি + হার = পরিহার, অনা + হার = অনাহার
‘কৃতি’ শব্দটির পূর্বে – যেমন – প্র + কৃতি = প্রকৃতি, আ + কৃতি = আকৃতি, বি + কৃতি = বিকৃতি, সু + কৃতি = সুকৃতি, নিঃ + কৃতি = নিষ্কৃতি, অনু + কৃতি = অনুকৃতি, দুঃ + কৃতি = দুষ্কৃতি, প্রতি + কৃতি = প্রতিকৃতি
‘কার’ শব্দটির পূর্বে – যেমন – আ + কার = আকার, বি + কার = বিকার, সম্ + কার = সংস্কার, প্র + কার = প্রকার, প্রতি + কার = প্রতিকার, উপ + কার = উপকার
‘গত’ শব্দটির পূর্বে – যেমন – আ + গত = আগত, প্র + গত = প্রগত, বি + গত = বিগত, পরা + গত = পরাগত, সম্ + গত = সংগত, নির্ (নিঃ) + গত = নির্গত, অব + গত = অবগত, অনু + গত = অনুগত, দুর্ (দুঃ) + গত = দুর্গত, অধি + গত = অধিগত
‘নত’ শব্দটির পূর্বে – যেমন – বি + নত = বিনত, অব + নত = অবনত, আ + নত = আনত, প্র + ণত = প্রণত, পরি + ণত = পরিণত
‘বাদ’ শব্দটির পূর্বে – যেমন -আ + বাদ = আবাদ, প্র + বাদ = প্রবাদ, অপ + বাদ = অপবাদ, সম্ + বাদ = সংবাদ, অনু + বাদ = অনুবাদ, বি + বাদ = বিবাদ, সু + বাদ = সুবাদ, পরি + বাদ = পরিবাদ, প্রতি + বাদ = প্রতিবাদ
একই ধাতুর পূর্বে ব্যবহার
‘কৃ’ ধাতুর অর্থ ‘করা’। যেমন √ কৃ + অ (ঘঞ্) = করা। ‘কৃ’ ধাতুর আগে বিভিন্ন উপসর্গ বসিয়ে বিভিন্ন অর্থের শব্দের উদাহরণ। যেমন – প্র – √ কৃ + অ (ঘঞ্) = প্রকার (রকম), বি – √ কৃ + অ (ঘঞ্) = বিকার (রূপান্তর / খারাপ অবস্থা লাভ), আ – √ কৃ + অ (ঘঞ্) = আকার (মূর্তি), সম্ – √ কৃ + অ (ঘঞ্) = সংস্কার (পরিষ্কার করা), অপ – √ কৃ + অ (ঘঞ্) = অপকার (ক্ষতি)
‘হৃ’ ধাতুর অর্থ ‘ হরণ করা’। যেমন √ হৃ + অ (ঘঞ্) = হার। ‘হৃ’ ধাতুর আগে বসিয়ে বিভিন্ন অর্থের শব্দের উদাহরণ। যেমন – প্র – √ হৃ + অ (ঘঞ্) = প্রহার (মার দেওয়া), আ – √ হৃ + অ (ঘঞ্) = আহার (ভোজন), উপ – √ হৃ + অ (ঘঞ্) = উপহার (পুরস্কার), বি – √ হৃ + অ (ঘঞ্) = বিহার (ভ্রমণ), সম্ – √ হৃ + অ (ঘঞ্) = সংহার (বিনাশ)
‘বদ্’ ধাতুর অর্থ ‘বলা’। যেমন √ বদ্+ অ (ঘঞ্) = বাদ। ‘বদ্’ ধাতুর আগে বসিয়ে বিভিন্ন অর্থের শব্দের উদাহরণ। যেমন – অপ – √ বদ্ + অ (ঘঞ্) = অপবাদ (নিন্দা), সম্ – √ বদ্ + অ (ঘঞ্) = সংবাদ (খবর), প্রতি – √ বদ্ + অ (ঘঞ্) = প্রতিবাদ (বিরুদ্ধে বলা), অনু – √ বদ্ + অ (ঘঞ্) = অনুবাদ (ভাষান্তর), অতি – √ বদ্ + অ (ঘঞ্) = অতিবাদ (বাড়িয়ে বলা), প্র – √ বদ্ + অ (ঘঞ্) = প্রবাদ (জনশ্রুতি)
উপসর্গ ও অনুসর্গের পার্থক্য
(i) উপসর্গ সব সময় ধাতু বা শব্দের আগে বসে কিন্তু অনুসর্গ দু’একটি ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণত বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে বসে।
(ii) ধাতু বা শব্দের সঙ্গে উপসর্গ এক হয়ে যায়। কিন্তু অনুসর্গ পূর্বের পদটির থেকে পৃথকভাবে অবস্থান করে।
(iii) ‘প্রতি’ ও ‘অতি’ ব্যতীত অন্য উপসর্গের স্বতন্ত্র প্রয়োগ নেই। অথচ অনুসর্গের স্বতন্ত্র প্রয়োগ আছে।
(iv) উপসর্গ ধাতু বা শব্দের আগে বসে সেই ধাতু বা শব্দের অর্থ-পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন শব্দ গঠন করে অন্যদিকে অনুসর্গ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের পরে বসে শব্দবিভক্তির কাজ করে।
শ্রেণিবিন্যাস
বাংলা ভাষার উপসর্গকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় – সংস্কৃত থেকে গৃহীত, বাংলা ও বিদেশি।
সংস্কৃত উপসর্গের প্রয়োগ
‘খ্যাত’ শব্দটির অর্থ বিখ্যাত বা প্রসিদ্ধ। ‘প্র’ যোগ করলে হয় ‘প্রসিদ্ধ’ (প্র +খ্যাত = প্রখ্যাত) যার দ্বারা ‘খ্যাত’ শব্দটির উৎকর্ষ সাধিত হয়। এইভাবে সৃষ্ট নতুন শব্দগুলির অর্থ বা অর্থের ভাব দেওয়া হলো।
প্র
উৎকর্ষ অর্থে = প্রভাব, প্রখ্যাত, প্রদান, প্রশংসা, প্রগতি, প্রতাপ, প্রভাত, প্রকৃষ্ট, প্রণত, প্রবুদ্ধ, প্রসাদ।
আধিক্য অর্থে = প্রকট, প্রচণ্ড, প্রবল, প্রগাঢ়, প্রখর, প্রচার, প্রলাপ, প্রসার, প্রকোপ।
আরম্ভ অর্থে = প্রদোষ, প্রবেশিকা, প্রবর্তন, প্রস্তাবনা।
বৈপরীত্য অর্থে = প্রস্থান, প্রবাসী।
পূর্ববর্তী অর্থে = প্রপিতামহ, প্রবীণ।
পরবর্তী অর্থে = প্রশিষ্য, প্রজন্ম, প্রপৌত্র।
অন্যান্য অর্থে = প্রক্ষেপ, প্রণিপাত, প্রকাশ, প্রকরণ, প্রয়াণ, প্রতাড়না, প্রদোষ, প্রবর্তন, প্রস্তাবনা।
পরা
আধিক্য অর্থে = পরাকাষ্ঠা, পরাক্রম, পরাক্রান্ত।
সম্যক অর্থে = পরামর্শ, পরায়ণ।
বৈপরীত্য অর্থে =পরাভব, পরাজয়, পরাঙ্মুখ, পরাবর্তন, পরাবৃত্ত।
অন্যান্য অর্থে অর্থে =পরাবিত্যা, পরাগ।
অপ
বৈপরীত্য অর্থে = অপকার, অপবাদ, অপমান, অপচয়, অপজ্ঞান, অপযশ, অপকীর্তি, অপলাপ, অপসংস্কৃতি।
নিন্দা / কুৎসিত অর্থে = অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপব্যবহার, অপভাষা, অপজাত, অপবাদ, অপমৃত্যু, অপধর্ম, অপদেবতা, অপশব্দ, অপপ্রয়োগ।
স্থানান্তরীকরণ অর্থে = অপনয়ন, অপসারন, অপহরণ, অপোনোদন, অপসৃত, অপনীত।
সম্
সম্যক অর্থে = সমাদর, সম্প্রদান, সমুচিত, সম্মান, সংকীর্তন, সম্পূর্ণ, সমীক্ষা, সংস্কার, সমাগত, সমালোচনা, সম্প্রদান, সন্তাপ, সংবেদন, সংজ্ঞা, সংবিৎ।
একতা অর্থে = সংকলন, সমাহার, সংহিতা, সংবাদ, সম্পর্ক, সমাবর্তন।
আভিমুখ্য অর্থে = সম্মুখ, সমক্ষে।
সত্বরতা অর্থে = সংবেগ।
নি
আতিশয্য অর্থে = নিদান, নিদারুণ, নিগূঢ়, নিতল, নিক্ষেপ।
সম্যক অর্থে = নিয়োগ, নিস্তব্ধ, নিরত, নিবিষ্ট।
বিরত অর্থে = নিবৃত্ত, নিষেধ, নিবারণ।
নিন্দা অর্থে = নিকৃষ্ট, নিগ্রহ।
ভিতরে অর্থে = নিমগ্ন, নিবাস, নিমজ্জন।
অভাব অর্থে = নিচ্ছিদ্র।
অন্যান্য অর্থে = নিবেশ উপনিবেশ, নিগম,নির্মাণ।
অব
বিরতি অর্থে = অবসর, অবকাশ, অবসন্ন, অবসাদ।
নিশ্চয় অর্থে =অবস্থান, অবধারণ, অবদান, অবগতি, অবরোধ, অবক্ষয়।
নিন্মতা অর্থে =অবগাহন, অবতারণ, অবরোহণ, অবনমন।
হীনতা অর্থে =অবনতি, অবজ্ঞাত।
বিযুক্ত অর্থে =অবচ্ছেদ, অবকাশ।
অনু
পশ্চাৎ অর্থে = অনুচর, অনুজ, অনুতাপ, অনুসরণ, অনুরাগ, অনুকরণ, অনুশোচনা, অনুস্বর, অনুচর, অনুগ।
আভিমুখিনতা অর্থে = অনুপ্রবেশ, অনুকূল।
সাদৃশ্য অর্থে = অনুরূপ, অনুদান, অনুগুণ, অনুলিপি।
পৌনঃপুনিকতা অর্থে = অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুধ্যান।
সম্যক অর্থে = অনুমোদন।
নির্ (নিঃ)
অভাব অর্থে = নির্দোষ, নির্ধন, নির্বংশ, নিরাশ, নির্লোভ, নিরানন্দ, নিরক্ষর, নিরাশ্রয়, নীরব, নীরত, নিশ্ছিদ্র, নিস্তরঙ্গ, নিরুপমা, নির্ভীক, নির্বাক, নিরন্ন, নিরুপমা, নিরাহার, নির্বেদ, নিরবলম্বন, নিরভিমান, নিরপরাধ।
সম্যক অর্থে =নির্দেশ, নিশ্চুপ, নিরীক্ষণ, নির্ণয়, নির্মুক্ত, নিষ্পিষ্ট, নির্ধারণ।
বহির্মুখিতা অর্থে =নির্গমন, নিঃসরণ, নির্গত, নিষ্কাশন।
দুর্ (দুঃ)
নিন্দার্থে = দুর্নাম, দুর্মুখ, দুঃশাসন, দুশ্চরিত্র, দুষ্প্রবৃত্তি, দুরাচার, দুরাশয়, দুরভিসন্ধি, দুষ্কৃতি,
অভাব অর্থে = দুর্ভিক্ষ, দুর্বল, দুষ্প্রাপ্য।
কষ্টকর অর্থে = দুর্গম, দুষ্কর, দুর্জয়, দুঃসাধ্য, দুরধিগম্য, দুরূহ, দিরুচ্চার্য।
বি
বৈপরীত্য অর্থে = বিপক্ষ, বিকৃতি, বিবাদ, বিয়োগ, বিক্রয়, বিধর্ম, বিরাগ।
সম্যক অর্থে = বিখ্যাত, বিজ্ঞান, বিস্তার, ব্যাঘাত, বিজয়, বিনিয়োগ, বিকাশ, বিচূর্ণ, বিন্যাস, বিনয়, বিনীত, বিবর্তন।
অভাব অর্থে = বিতৃষ্ণা, বিনিদ্র, বিবস্ত্র, বিবর্ণ।
প্রতিক্রিয়া অর্থে = বিক্রিয়া।
আতিশয্য অর্থে = বিশ্রান্ত (অতিশয় শ্রান্ত)