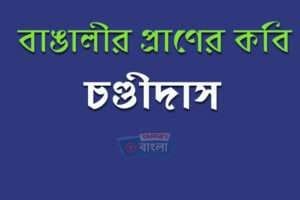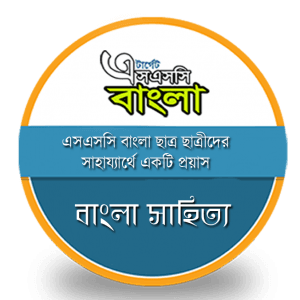মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম ধারা পদাবলি সাহিত্য। পদাবলি সাহিত্যের ধারায় বৈষ্ণব পদাবলি -এর কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পদাবলি সাহিত্যগুলিতে যেমন কবির ভক্তিভাব প্রকাশিত তেমনি সমাজের নানা দিকও প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের এই আলোচনা মূলত বৈষ্ণব পদাবলির কয়েকজন কবি সম্পর্কে।
বৈষ্ণব পদাবলি – বিদ্যাপতি
(১) সংক্ষিপ্ত পরিচয় – মিথিলারাজ শিবসিংহের সভাকবি বিদ্যাপতির জন্ম চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। তাঁর তিরোভাব ঘটে পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আনুমানিক ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি। বিদ্যাপতি চৈতন্য-পূর্ব পদকর্তা।
(২) বিদ্যাপতির গ্রন্থ পরিচয়ঃ সময়কাল সহ
ভূপরিক্রমা (১৪০০ খ্রিঃ কাছাকাছি), পুরুষপরীক্ষা (১৪১০), কীর্তিপতাকা (১৪১০), লিখনাবলী (১৪১৮), শৈবসর্বস্বহার (১৪৩০ – ১৪৪০), গঙ্গাবাক্যাবলী (১৪৩০ – ১৪৪০), বিভাগসার (১৪৪০ – ১৪৬০), দানবাক্যাবলী (১৪৪০ – ১৪৬০), দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী (১৪৪০ – ১৪৬০)
(৩) পদ সংখ্যা – রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আছে এমন পদ ৫০০টিরও বেশী ।
Looking for PDF? Click here
(৪) অভিনব জয়দেব – আসলে বিদ্যাপতির কাব্যে জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যের প্রভাব আছে। বিশেষত রাধা চরিত্র নির্মাণে জয়দেবের প্রভাব লক্ষিত হয়।
(৫) মৈথিলী কোকিল – মিথিলার এই কবি তার পদাবলির সুমিষ্ট আবেদনে বাঙালি কাব্য পাঠকের মনকে সহজেই দ্রবীভূত করতে পারেন।
(৬) বিদ্যাপতি নিজেকে মধ্যযুগের ‘কবি সার্বভৌম’ ও ‘খেলন কবি’ বলেছেন তাঁর ‘কীর্তিলতা’ কাব্যে।
(৭) বিদ্যাপতিকে বাংলা সাহিত্যে অন্তর্ভুক্তির কারণ – মিথিলার কবি হলেও বিদ্যাপতি বাঙালির হৃদয় রাজ্যে অধিষ্ঠিত। আসলে মিথিলার সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতা, বিদ্যাপতির ওপর জয়দেবের প্রভাব, তাঁর পদ চৈতন্যদেব কর্তৃক আস্বাদন এই সমস্ত কারণে বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতি অমর হয়ে আছেন।
(৮) বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব – বিদ্যাপতি জীবন রস রসিক যৌবনের কবি, প্রেমের কবি। তার পদে লৌকিক সংসারের প্রণয়াসক্ত নরনারীর মিলন বিরহের আর্তি ফুটে উঠেছে। রাধা চরিত্র নির্মাণে কবি তার মনস্তত্ব ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন
(৯) বিদ্যাপতি রচিত পদের ভাষা – ব্রজবুলি
(১০) ব্রজবুলি – ব্রজবুলি কোনো অঞ্চলের ভাষা নয়। বাংলা, মৈথিলি ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট একটি কৃত্রিম লেখ্য ভাষা ।
চণ্ডীদাস
(১) চণ্ডীদাস সম্পর্কে প্রথম বিস্তারিত আলোচনা করেন – রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর ‘বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব’ গ্রন্থে।
(২) চণ্ডীদাসের জন্ম – চণ্ডীদাসের জন্ম বীরভূমের নান্নুর গ্রামে। মতান্তরে বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামে।
(৩) চণ্ডীদাসের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ লেখেন – কৃষ্ণপ্রসাদ সেন। গ্রন্থটিকে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রবাসী কার্যালয় থেকে প্রকাশ করেন ।
(৪) চণ্ডীদাস যে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি তার প্রমাণ – শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে “বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ / এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ’।
(৫) চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব – চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব আক্ষেপানুরাগের পদে। উদাহরণ – রাতি কইনু দিবস, দিবস কইনু রাতি / বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরিতি
(৬) চণ্ডীদাস সমস্যা জোরালো হয়ে ওঠে – শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কাব্য আবিষ্কারের পর
জ্ঞানদাস
(১) সংক্ষিপ্ত পরিচয় – চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তা। জন্ম বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী কাঁদরা গ্রামে। আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে মোটামুটি ১৫৩০ খ্রিঃ। তিনি ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষাতে পদ রচনা করেছেন । তবে তাঁর কৃতিত্ব যা কিছু তা বাংলা পদকে কেন্দ্র করেই।
(২) পদ সংখ্যা – ‘পদকল্পতরু’তে জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্ত পদ পাওয়া যায় ১৮৬ টি। যার মধ্যে ব্রজবুলি পদ ১০৫টি আর বাংলা পদ ৮১টি।
(৩) জ্ঞানদাসকে কার ভাবশিষ্য বলা হয় – চণ্ডীদাসের
গোবিন্দদাস
(১) সংক্ষিপ্ত পরিচয় – গোবিন্দদাস চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তা। জন্ম ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশকে। তিনি প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন পরে ৪০ বছর বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন ।
(২) শাব্দিক কবি কেন – তাঁর পদে শব্দ ও অনুপ্রাসের ঝংকার আছে। যেমন – নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
(৩) দ্বিতীয় বিদ্যাপতি কেন – তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষাকে। বিদ্যাপতির মতো তার কাব্যেও ব্রজবুলির ব্যবহার ঘটেছে।
(৪) পদ সংখ্যা – প্রায় ৮০০টি
(৫) শ্রেষ্ঠ পর্যায় – অভিসার
(৬) নাটক – সঙ্গীতমাধব
(৭) গোবিন্দদাসকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলেছেন – বৈষ্ণব পদকর্তা বল্লভদাস ।
(৮) গোবিন্দদাসকে কবিরাজ উপাধি দিয়েছেন – এ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন শ্রীনিবাস আচার্য আবার কেউ বলেন শ্রীজীব গোস্বামী
(৯) পদের বৈশিষ্ট্য – ঝংকার মুখর ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার, ছন্দের বিস্ময়কর কারুকাজ, চিত্রকল্পের প্রয়োগ, কল্পনা ও আবেগের সুনিপুণ প্রয়োগ
বৈষ্ণব পদাবলি সংক্রান্ত আরো কিছু তথ্য
(১) বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী – সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস, ও রঘুনাথ ভট্ট।
(২) বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীদের লেখা গ্রন্থ –
সনাতন গোস্বামী – বৃহদ ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, বৈষ্ণবতোষণী
শ্রীরূপ গোস্বামী – হংসদূত, উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
(৩) মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের সংস্কৃত জীবনী কাব্য –
মুরারী গুপ্তের “শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত’ যা মুরারী গুপ্তের কড়চা নামে পরিচিত।
কবিকর্ণপুর বা পরমানন্দ সেনের ‘চৈতন্য চরিতামৃত’, ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা
প্রবোধানন্দ সরস্বতীর চৈতন্যচন্দ্রামৃত
স্বরূপ দামোদরের কড়চা
(৪) খেতুরী মহোৎসব – নরোত্তম ঠাকুর ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে বৈষ্ণব সম্মেলনের আহ্বান করেন তাই খেতুরী মহোৎসব। খেতুরী বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহীতে অবস্থিত।
(৫) বৈষ্ণব পদাবলির শ্রেষ্ঠ সংকলন গ্রন্থের নাম – গোকুলানন্দ সেনের ‘পদকল্পতরু’। [অন্যান্য সঙ্কলন গ্রন্থ সম্পর্কে দেখুন]